Abosar
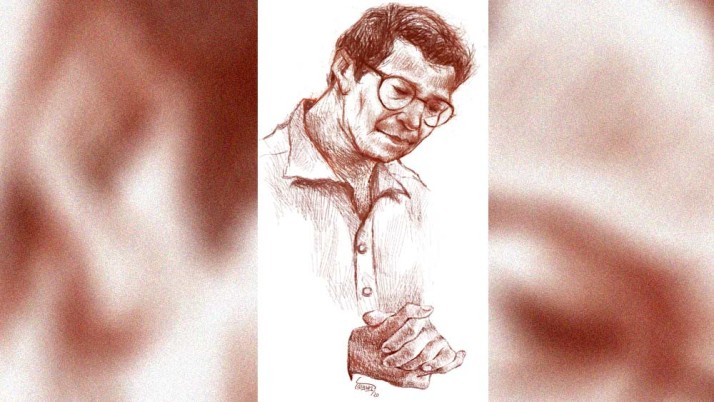
খালাস
সৌরভ মুখোপাধ্যায়
হঠাৎ দেখা— এই ব্যাপারটা গল্প তৈরির কাজে এত বার লেগেছে আদ্যিকাল থেকে যে, এ জমানায় ওটার তেমন অভিঘাত নেই আর। পত্রপত্রিকায় এ রকম কো-ইনসিডেন্স টাইপ গল্প-উপন্যাস দেখলে আমার হাই ওঠে আজকাল।
কিন্তু আজ যা ঘটল, তা তো আর গল্প নয়। তাই, প্রথম যখন টেবিলের ও পাশের দু’টো চোখে আমার চোখ মিলল, একটা চকিত ঝাঁকুনি খেয়ে কয়েক সেকেন্ড আমার সারা শরীর নিশ্চল হয়ে গিয়েছিল। হয়তো স্নায়ুগুলো ঢিলে ছিল বলেই ধাক্কাটা জোর লাগল অত!
হ্যাঁ, সারা দিনের একটানা ধকলে শ্রান্ত ছিলাম খুব। অফিসে কাল প্রায় সারা রাত জেগেছি, আবার আজ সেই ভোর থেকে পোলিং ডিস্ট্রিবিউশন সেন্টারে রগড়ানি চলছে। কাল ভোট। কয়েক হাজার ভোটকর্মীকে এই সেন্টার থেকে মালপত্র-সমেত বিভিন্ন প্রান্তে পাঠানোর রাজসূয় যজ্ঞ আজ। পাঁচটা নির্বাচনক্ষেত্রের পাঁচখানা আলাদা প্যান্ডেল, প্রতিটিতে বিশ-বাইশখানা কাউন্টার। শয়ে শয়ে ভোটকর্মীদের পোলিং মেটিরিয়াল গুনেগেঁথে দেওয়া। ছুটকো ইসুতে ভোটকর্মীদের ফোঁস-ফোঁস গর্জনের অন্ত নেই। বাস-ট্রেকার-অটো সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে পাশের মাঠে, তাদের নিয়ে হাজার বায়নাক্কা। পুলিশ-ক্যাম্পেও নিত্যনতুন ঝামেলা লেগেই আছে। সকাল ন’টা থেকে সন্ধে সাতটা পর্যন্ত এই বিপুলায়তন তেরপল-প্যান্ডেলের নীচে সহস্র লোকের সাড়ে বত্রিশ ভাজা, চিৎকার-দাপাদাপি, জ্যৈষ্ঠ মাসের এই নির্মম তাপের মধ্যে— ভয়াবহ ব্যাপার!
তার ওপর, এ আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। বড় চাকরির পরীক্ষার শেষ গ্রুপটায় উতরে, মাঝারি র্যাঙ্কের একটা অফিসার হয়ে ব্লকে জয়েন করেছি সবে বছরদেড়েক, বেজে গেল ভোটের বাদ্যি, আর পাকেচক্রে হয়ে গেলাম এই বিতরণকেন্দ্রের এআরও— অ্যাসিস্ট্যান্ট রিটার্নিং অফিসার। পাঁচখানা তেরপল-শিবিরের মধ্যে, এই একখানির গোটা ওজন ঘাড়ে নিয়ে ঘুরছি। এই বিশেষ প্যান্ডেলটিতে যে ভূতের বাপের বিবাহব্যাপার, তাতে আমিই বরকর্তা। পান থেকে চুন খসলে আমারই দায়, কৈফিয়ত চাইবেন রিটার্নিং অফিসার স্বয়ং! সারা দিনের চরকিপাক আর চেঁচামেচির ঠেলায় শরীর আর মগজ দুই-ই ক্লান্তির শেষ সীমায় পৌঁছেছে।
সন্ধের মুখে আমার প্যান্ডেল একটু ফাঁকা হল। পোলিং পার্টি সব বেরিয়ে গেছে। একটু হাঁপ ছেড়ে চেয়ারে গা এলিয়েছি, কিছুটা দূরে বসে আমার ডিপার্টমেন্টের হেড ক্লার্ক রমেশ পোদ্দার বলল, “ওফ! সুস্থ লোককে পাগল করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট, কী বলেন দাসসাহেব?”
‘পাগল’ শব্দটা শুনলেই আমি কেমন চমকে উঠি। এখনও উঠেছিলাম। তার পর, নিজের মনে হেসে ফেলেছিলাম সঙ্গে সঙ্গেই। হেড ক্লার্ক আমার হিস্ট্রি জানে না।
নতুন করে পাগল আর কী-ই বা হব? পাগল থেকেই সুস্থ হয়েছি তো।
আজ পরীক্ষা পাশ করে অফিসার হয়েছি, অফিসে ঊর্ধ্বতন অধস্তন সবাই ‘দাসসাহেব’ বলে ডাকে— কিন্তু আঠাশ বছরের শুভময় দাস কি অত সহজে ভুলতে পারবে তার আট বছর আগেকার সেই পুরনো নাম? ‘পাগলা শুভো’?
তখন কলেজের সেকেন্ড ইয়ার, আমি পাগল হয়ে গিয়েছিলাম।
সত্যিকারের পাগল। আজকের এই টিপটপ ক্লিনশেভন ডিয়ো-সুবাসিত দাসসাহেবকে দেখে কেউ কল্পনা করতে পারবে না সেই ‘আট বছর আগের একদিন’।
সারা রাত জেগে, আয়নার সামনে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে বসে থাকতাম। চুপি চুপি সদর দরজার খিল খুলে রাস্তায় বেরিয়ে যেতাম নিশুত অন্ধকারে। ল্যাম্পপোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে থাকতাম। বৃষ্টি শুরু হত, বাজ পড়ত, আমার ভ্রুক্ষেপ হত না। বোধ নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, মগজটা বেবাক ফাঁকা। স্নান করতাম না, জামা-প্যান্ট বদলাতাম না, চুলে জট, সারা মুখে কুটকুটে দাড়ি, গায়ে চিট ময়লা। সারা দিন ঘুরতাম জলায়-জাঙালে শ্মশানে-মশানে। শুধু যখন প্রচণ্ড খিদেয় গা গুলোত, বাড়ি ফিরে মাকে বলতাম, “খেতে দাও!”
আমার বিধবা মা আমার বুকে মাথা কুটে কুটে কাঁদত, বলত, “শুভো, বাবা আমার, তোর কী কষ্ট আমাকে বল!”
আমি নিরুত্তাপ গলায় বলতাম, “কষ্ট নেই তো!”
“তবে হঠাৎ কী হল, এত ভাল মাথা তোর… এমন করছিস কেন বাবা?”
“মা, আমার কোনও কষ্ট নেই— এটাই আমার কষ্ট, জানো?” আমি বিড়বিড় করতাম, “আমি খুব তীব্র ভাবে কষ্ট পেতে চাই, এফোঁড়-ওফোঁড় কষ্ট… কিন্তু পাচ্ছি না কিছুতেই, বুঝলে…”
‘পাগলা শুভো’। নামটা তত দিনে সেঁটে গেছে গায়ে। রাস্তায় বেরোলে বাচ্চারা চেঁচাত ওই বলে।
তা, পাগলও ভাল হয়। আমিও হলাম এক দিন।
পাড়ার লোক আর আত্মীয়রা মিলে জোর করে ডাক্তারের কাছে নিয়ে গিয়েছিল, ওষুধ খেয়ে ঘরে বসে ঝিমোতাম। এ রকম কতকাল গেছে খেয়াল ছিল না, তার পর আস্তে আস্তে মাথায় সাড় ফিরল বুঝি। এক দিন দেখি, চারপাশটা অন্য রকম ঠেকছে। সকলে বলতে লাগল, আমি ভাল হয়ে গেছি।
পাগল থাকাকালীনও যে মন্দ কিছু ছিলাম, এমন বোধ হয়নি কখনও। সেরে উঠেও দিব্যি লাগল। চুলদাড়ি কাটা হল, সাফসুতরো পোশাক। লোকে এসে পিঠ চাপড়ে উৎসাহ দিতে লাগল। অনেকগুলো দিন পাগল ছিলাম, তার দরুন এখন যে নতুন কোনও অসুবিধে হচ্ছিল, এমন নয়। অনুভবটা এক কথায় অন্যকে বোঝানো কঠিন। যেন অজানা বিদেশ ঘুরে বাড়ি ফিরলাম! কিংবা, যেন একই দুনিয়া— দুধেলা চাঁদের আলোয় দেখছিলাম এত দিন, এখন ফের শরৎ-দুপুরের মিহিন রোদ।
বইপত্র উল্টে দেখলাম, বেশ ফুরফুরে ঠেকল, স্মৃতিও কাজ করছে, বাহ! এক বছর ড্রপ, তার পর কলেজের শেষ পরীক্ষাটা সাদামাঠা ভাবে পাশও করি। পাগলা শুভো গ্র্যাজুয়েট। বেশ ভাল ব্যাপার।
তার পর, কেন কে জানে, কী এক খেয়াল চাপল, চাকরি পেতে হবে। পেতে হবে তো পেতেই হবে। হয়তো এও পাগলামিরই অন্য রূপ— আমি আদাজল খেয়ে শুধুই চাকরির পরীক্ষার জন্য পড়তে লাগলাম। এত দিনে টের পাচ্ছিলাম, তফাত একটা কিছু ঘটেই গেছে আমার মাথার মধ্যে, কিছু একটা ওলটপালট! পাগলা শুভোর ছিল নির্বিকার ঔদাসীন্য, সেরে-ওঠা শুভোর মধ্যে ধীরে ধীরে জন্মাচ্ছে একটা অন্ধ জেদ!
বদলাতে লাগলাম নিজেকে। সারা দিন ঘষতে শুরু করলাম। ইংরেজি অঙ্ক ভাল জানতাম, জিকে আর কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সের বই গুলে খেলাম, সংবিধান আর ইতিহাস-ভূগোল কণ্ঠস্থ করলাম। মেন্টাল আপ্টিচিউড, নিউমেরিকস, আরও সব হাবিজাবি। স্পোকেন ইংলিশ রপ্ত করলাম। পরীক্ষার পর পরীক্ষা, যা দেখতে পাই চোখের সামনে। স্টেট, সেন্ট্রাল, রেল, ব্যাঙ্ক, পোস্টাল, স্কুল সার্ভিস। কিন্তু অতই কি সহজ? হয় না, হয় না! তার পর তিন বছরের মাথায় একটা-দু’টো রিটনে উতরোলাম, ইন্টারভিউয়ে হল না। কিংবা প্রিলিমিনারি পাশ করে মেন পরীক্ষায় আটক। পুরোটা ক্লিক করছে না এক বারও! তবু লেগে থাকি, নাছোড়।
এই করতে করতে, এই বড় পরীক্ষাটার নীচের দিকের গ্রেডটা ফস করে লেগে গেল। রিটনেও, ভাইভাতেও! ব্যস, এই হল কিসসা। পাগলা শুভো বন গয়া অফ্সর!
তপ্ত দুধ জুড়িয়ে এলে পুরু সর পড়ে। আমার পাগল হয়ে যাওয়ার ইতিহাসটুকু এখন সাফল্য আর পদমর্যাদার নীচে চাপা।
হেড ক্লার্কের মুখে ওই ‘পাগল’ কথাটা শুনেই অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিলাম একটুখানি। হঠাৎ শুনতে পেলাম, একটু দূরে রিজ়ার্ভ পোলিং অফিসারদের কাউন্টারে একটা শোরগোল চলছে। কাউন্টারের কর্মীদের সঙ্গে কথাকাটাকাটি চলছে ও পাশের কারও।
প্যান্ডেলের বাইরে অন্ধকার, ভেতরে আলোগুলো জ্বলে উঠেছে সব। রেগুলার পোলিং পার্সোনেলদের নিয়ে বাস-ট্রেকার সব বোঝাই হয়ে চলে গেছে গন্তব্যে। এখন এই প্যান্ডেলের একটিমাত্র কাউন্টারেই শুধু ব্যস্ততা, কারণ এখনও রয়ে গেছে রিজ়ার্ভ ভোটকর্মীরা। কোথাও দরকার হলে তাদের পাঠানো হবে। নির্দেশ আছে, এদের রাতে এখানেই থাকার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু অনেকেই থাকতে চাইছিল না। কাউন্টারে ভিড় করে অনুরোধ করছিল, যেন তাদের ছেড়ে দেওয়া হয়, তারা বাড়ি যাবে। কার শরীর খারাপ, কার বাড়িতে খুব দরকার— নানা অজুহাত। আমাদের ওপরমহল থেকে কড়া আদেশ আছে, প্রবলতম এমার্জেন্সি ছাড়া কোনও রিজ়ার্ভ কর্মীকে রিলিজ় দেওয়া চলবে না। সকলকে আগামী কাল দুপুর পর্যন্ত আটকে রাখতেই হবে।
কাউন্টারের সাধারণ কর্মীদের কোনও এক্তিয়ারই নেই রিলিজ দেওয়ার। রিটার্নিং অফিসারই তা পারেন, তাঁর অনুপস্থিতিতে সেই অধিকার একমাত্র আমার, এই শিবিরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক আমি। কর্মীরাও তা-ই বলেই উল্টো দিকের অনুনয়কারীদের ভাগিয়ে দিয়েছে স্ট্রেট, “এআরও সাহেব পারমিশন না দিলে কিছু হবে না। কাউকে ছাড়ার আইন নেই… যান, যান এখান থেকে…”
ভিড় পাতলা হয়েও গিয়েছিল।
কিন্তু এখন ফের কেউ এক জন কাঁদুনি গাইতে এসেছে মনে হচ্ছে। কাউন্টারের ও পাশে একটা কণ্ঠ শোনা যাচ্ছে, “তা হলে একটু সাহেবের সঙ্গেই দেখা করতে দিন আমাকে… আমার খুব দরকার…”
“কেন ফালতু ঝামেলা করছেন? সাহেব কাউকে রিলিজ় দেবেন না… যান… সাহেব এখন ব্যস্ত আছেন…”
“প্লিজ় এক বার ওঁকে খবরটা অন্তত দিন, না হলে আমাকে এক বার দেখা করতে…”
শিক্ষিত লোকের গলা মনে হল, মার্জিত কিন্তু কাতর স্বর। মনে হল, এক বার ব্যাপারটা দেখে আসাই দরকার। সত্যিই যদি প্রচণ্ড দরকার কিছু হয়েই থাকে, শরীর-টরির খারাপ ইত্যাদি— জেদ করে আটকে রেখে আমিই ফেঁসে যাব শেষমেশ। পোদ্দারও তাই বলল, “হ্যাঁ স্যর, মেডিক্যাল এমার্জেন্সি-টেন্সি হলে ঝামেলা হবে চাট্টিখানিক। এক বার দেখে অন্তত আসুন, বেগতিক হলে আরও-কে রেফার করে দেবেন…”
“কী হয়েছে? কী ব্যাপার এখানে, বলুন? কী চাই?” পদাধিকারের ভারিক্কি বাটখারাগুলো আওয়াজের পাল্লায় চাপিয়ে কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেলাম। কাউন্টারের ও পাশে চশমা-পরা একটি মাঝবয়সি মুখ দেখতে পেয়েই সরাসরি বলে দিই, “কী চাই? কাউকে ছাড়া যাবে না… থাকতে হবে…”
“দয়া করে আমার কথাটা একটু…” বলতে বলতে চশমার ও পারে দুটি চোখ স্থির হয়ে যায়।
এ পারে, আমিও, স্তব্ধ।
সুজাতাকে প্রথম দেখেছিলাম ফার্স্ট ইয়ারেই, পিআরসি-স্যরের কাছে পড়তে গিয়ে। আগাগোড়া মেয়েদের স্কুল-কলেজে পড়া সুজাতা পারতপক্ষে ছেলেদের সঙ্গে কথা বলত না। ব্যাচের মধ্যে আমার সঙ্গেই সম্ভবত তার প্রথম আলাপন। প্রথম দিন সে আমাকে ‘আপনি’ বলে কথা বলেছিল, “আপনার খাতাটা এক দিনের জন্যে দেবেন?” গোটা ব্যাচ হেসে উঠেছিল, পিআরসি-ও। সদ্য কলেজ-সার্ভিস পাশ তরুণ শিক্ষকটি ছাত্রদের সঙ্গে বন্ধুর মতোই হাসিঠাট্টা করতেন। বলেছিলেন, “এক সপ্তাহের মধ্যে তুইতোকারি চালু হবে, সে দিন আমি মিষ্টি খাওয়াব!”
না, অত নিখুঁত অবিশ্যি মেলেনি স্যরের কথা। এক সপ্তাহ নয়, ঠিক এক মাস পরে— সুজাতা আমাকে ‘তুই’ বলেছিল। আমার সিঁড়ির ঘরে, সেই প্রথম বার, আমাকে চুমু খেতে খেতে। আশ্লেষের উন্মাদনায় চোখ বুজে গিয়েছিল তার, কচি কদম্বরেণু ফুঁড়ে উঠেছিল সারা দেহে। নিজের তীব্র তাপ আমার কোষে-কোষে ছড়িয়ে দিতে-দিতে সে অস্ফুটে কেবলই বলছিল, “শুভো তুই আমাকে ছাড়বি না কখনও, ছাড়বি না বল শুভো…”
“ছাড়ব না রে, কক্ষনও না…” দু’হাতের বেড়ে শক্ত করে নিজের সঙ্গে পিষে নিচ্ছিলাম আমি সুজাতাকে, যেন আঠা দিয়ে, ঝালাই করে, জুড়ে নিতে চাইছিলাম বরাবরের মতো!
তার পাক্কা এক বছর বাদে, গোলাপি ডানায় তরতরিয়ে ভেসে-যাওয়া বারোটি মাস কেটে যাওয়ার পর— এক দিন, আচমকা, আমি পাগল হয়ে গেলাম!
কী ভাবে কী ঘটেছিল, তার ব্যাখ্যা আজও নেই আমার কাছে। শুধু, সুজাতা আমাকে এড়িয়ে চলছে কিছু কাল, এর বেশি কিছু বুঝতে পারছিলাম না। তার পর, এক দিন পিআরসি-র বাড়িতে একটু অসময়ে গিয়ে পড়েছিলাম একটা বইয়ের খোঁজে। আগেও এমন গেছি বহু বার। কিন্তু সে দিন পর্দাটা সরাতেই…
আশ্চর্য, দু’জনের কেউই তেমন অপ্রস্তুত হয়নি। স্যর একটু গলাখাঁকারি দিয়ে বেশ সপ্রতিভ ভঙ্গিতেই বলেছিলেন, “ওয়েল, হোয়াটএভার হ্যাপেনস… শুভো, এ এক রকম ভালই হল। দ্য সুনার ইউ আর ফেসড উইথ দ্য ট্রুথ, দ্য বেটার!”
আমি তাঁর দিকে ফিরে তাকাইনি পর্যন্ত। শুধু অপলকে সুজাতাকে দেখছিলাম। এটাই আমায় বেশি বিমূঢ় করছিল যে, তার চোখে অনুতাপের মেঘ নেই, খটখটে শুকনো নির্লিপ্তি ছাড়া আমার জন্যে সেখানে আর কিচ্ছুটি ছিল না। মরসুম এমন আমূল বদলে গেল, আমার সম্পূর্ণ অগোচরে! এত দিন তবে কী করছিলাম আমি, শুভো ভ্যান উইংকল…!
না, একেবারে চুপ করেও থাকেনি সুজাতা। শীতল, শুকনো গলায় বলেছিল, “শুভো আমাকে মাফ করে দিস। আগে তোকে বলা হয়নি… বাট নাও ইউ নো… লিভ মি, প্লিজ়।”
আমি তার চোখ থেকে চোখ না সরিয়ে, পাথর-হয়ে-যাওয়া জিভটা নেড়েছিলাম, “ছাড়তে… বারণ করেছিলি না!”
সুজাতা চুপ করে গিয়েছিল হঠাৎ। চোখ নামিয়ে ফেলেছিল। পিআরসি নিজে সোফা থেকে উঠে এসেছিলেন আমার সামনে। কাঁধে হাত রেখেছিলেন, “ছেড়ে দিতেও জানতে হয় শুভো…”
আমি খুব ঘৃণাভরে রোমশ ফর্সা হাতটাকে দু’আঙুলে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে, তার পর বুকের খাঁচা থেকে সমস্ত বাতাস, নাকি আগুন… উগরে দিতে-দিতে বলেছিলাম, “ছে-ড়ে দে-ব? ভাবলেন কী করে? শুভময় দাস আপনাদের কা-উ-কে ছাড়বে না জেনে রাখুন! নে-ভা-র!”
কাউন্টার থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছি দ্রুতপায়ে। এ বার একেবারে সামনাসামনি। দু’জনে দু’জনের চোখের দিকে তাকিয়ে আছি। কে আগে পলক ফেলবে?
উনিই ফেললেন। মাথাটা নামিয়েও নিলেন। আমি বুঝলাম, ভূমিকার দরকার ফুরোল।
“এনিথিং রং, স্যর?”
কেঁপে উঠলেন কি? মুখটা কি নীরক্ত হল মুহূর্তের জন্য? বোঝা গেল না ঠিক। সেই নতশির অবস্থাতেই খুব নিচু গলায়, ঠোক্কর খেতে খেতে বললেন, “আ-আমি… মানে… ইট’স আর্জেন্ট… বাড়িতে… অ্যাকচুয়ালি…” একটু থেমে ফের বললেন, “শি ইজ় নট ওয়েল…”
“কেন, কী হয়েছে?”
“নার্ভের… ইয়ে… মানে, অনেক দিনই। তিন বার মিসক্যারেজ… তার পরই…” স্বর আরও নেমে এল, “স্কিৎজ়োফ্রেনিয়া… রেগুলার মেডিক্যাল সুপারভিশন লাগে। গত তিন বছর… টোটালি শ্যাটার্ড, ইন ফ্যাক্ট। বাইরে কোথাও রাত কাটাতে পারি না আমি। আমার ফেরাটা… খুবই…মানে…”
চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। বাইরে একটা হালকা ঝোড়ো হাওয়া বয়ে গেল এক ঝলক। তেরপল-ছাউনির কাঠামো মৃদু মড়মড় শব্দ করল। গ্রীষ্মসন্ধ্যার কালো আকাশে কি এক চিলতে নীল বিদ্যুতের চেরা জিভ চমকাচ্ছে থেকে থেকেই? কালবৈশাখীর পূর্বাভাস ছিল কি না, মনে পড়ল না।
আমি একেবারে নির্বাক নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি, অনেক বছর পর আমার মগজটা ফের যেন ফাঁকা হয়ে, স্থবির হয়ে, থেমে আছে কয়েক পল, নাকি কয়েক যুগ!
তার পর দেখতে পেলাম, সামনের ছায়ামূর্তিটা, নীরবেই, ধীর পায়ে সরে যাচ্ছে। কিছু দূরে অন্ধকার একটা কোণ, সেই দিকে। ঝুঁকে পড়েছে যেন একটু।
ডাকি। বলি, “শুনুন! আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা?”
দ্বিধাগ্রস্ত ভঙ্গিতে উনি ফেরেন, বাড়িয়ে ধরেন কাগজটা। আমি একটু চোখ বুলিয়ে নিতে থাকি, উনি আমার সামনে দাঁড়িয়ে। মাথা নিচু।
আমি পকেট থেকে দামি কলম বার করে, ধীরেসুস্থে কাগজটার ওপর গোটা-গোটা করে কয়েকটা ইংরেজি অক্ষর লিখি।
পোদ্দারকে ডেকে সিল লাগাতে বলি। স্বাক্ষর করি। শুভময় দাস।
তার পর নিজের মসৃণ গালে এক বার হাত বুলিয়ে, পাঁচ আঙুলে চুলগুলো সেট করে নিই এক বার। টানটান হয়ে দাঁড়াই। নিঃশব্দেই স্মার্ট হাসি গড়িয়ে দিই এক চিলতে। বিলিতি কলমটা খুব কায়দা করে গুঁজি বুকের বাঁ দিকের পকেটে। বাইরে এখন ঠান্ডা হাওয়া দিচ্ছে, আকাশ শান্ত, তারা ফুটেছে। বৃষ্টিটা দূরে কোথাও হয়ে গেল বোধহয়।
খালাসপ্রাপ্ত রিজ়ার্ভ ভোটকর্মী প্রদীপ্তরঞ্জন চৌধুরী তাকিয়ে রয়েছেন। তাঁর দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে হালকা গলায় বলি, “যান, রিলিজ়ড। সুজাতাকে বলবেন।”